শচীন টেন্ডুলকারের অটোবায়োগ্রাফী “প্লেয়িং ইট মাই ওয়ে” প্রকাশিত হয় ২০১৫ সালে। বাংলায় অনুবদের কাজটা করেছিলাম আমি। এই লেখাটি সেই বইয়ের প্রথম অধ্যায়।
শচীনের শৈশব

“বাবা, জীবনটা একটা বইয়ের মত। অনেকগুলো অধ্যায় আছে এতে। বইয়ের মতই শিক্ষাও আছে অনেক। অনেক ধরনের অভিজ্ঞতায় ভরা আমাদের জীবন। পেন্ডুলাম একবার সফলতার দিকে দুলবে, আরেকবার দুলবে ব্যর্থতার দিকে। সাফল্য, ব্যর্থতা, দু’টোরই আলাদা আলাদা শিক্ষা আছে। দু’টো থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। তবে বেশীরভাগ সময়ই সফলতার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার চেয়ে, ব্যর্থতার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাই বেশি মূল্যবান। তুমি একজন ক্রিকেটার বা ক্রিড়াবিদ। তুমি তোমার দেশকে প্রতিনিয়ত বিশ্বের সামনে তুলে ধরছ। বলাবাহুল্য এ এক বিরাট সম্মান। কিন্তু কখনও ভুলে যেওনা এটাও জীবনের একটা অধ্যায় মাত্র। একটা মানুষ কতদিন বাঁচবে? বড় জোড় সত্তুর বা আশি বছর। এর মধ্যে তুমি খেলবে কত বছর? বিশ, খুব ভালো খেলতে পারলে হয়তো বা পঁচিশ, তার বেশি নয়। তারমানে কি? তোমার জীবনের বেশির ভাগটাই কাটবে ক্রিকেটের বাইরে। সোজা কথা হল, জীবনটা ক্রিকেটের চেয়েও অনেক বড়। শোন বাবা, আমি চাই তুমি ভারসাম্য রাখতে শেখো। তোমার সাফল্য যেন তোমাকে দাম্ভিক করে না তোলে। যদি বিনীত, নম্র থাকো তাহলে তোমার ক্রিকেটারের ছোট্ট জীবনটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও মানুষ তোমাকে সম্মান করবে, ভালোবাসবে। একজন বাবা হিসেবে, “শচীন একজন ভালো খেলোয়াড়” এর চেয়ে “শচীন একজন ভালো মানুষ”Ñএটা শুনতেই বেশি ভালো লাগবে আমার।”
কথাগুলো আমার বাবার। বেড়ে ওঠার সময় অগণিতবার এই কথাগুলো শুনেছি আমি। আমার জীবনদর্শন এই কথাগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।
আমার জন্ম মুম্বাইয়ের পূর্ব বান্দ্রায় এক রক্ষণশীল মহারাষ্ট্রীয় পরিবারে। থাকতাম সাহিত্যিরা সাহাওয়াস কলোনীতে। আমাদের কলোনীটা লেখকদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জুৎসই একটা জায়গা কিন্তু আমি হয়ে গেলাম ক্রিকেটার। চার ভাই বোনের মধ্যে সবার ছোট আমি। আমার বড় দু’ভাই আর এক বোন। ভাইদের নাম অজিত আর নিতিন আর বোনের নাম সাবিতা। আমি যে শুধুমাত্র বাড়ির সবচেয়ে ছোট সদস্যই ছিলাম না, বাড়ির সবচেয়ে দুষ্টু সদস্য বলতেও আমাকেই বোঝানো হত।
আমার বাবা রমেশ টেন্ডুলকার, সুপরিচিত মারাঠি কবি, সাহিত্য সমালোচক, অধ্যাপক। আর মা, রজনী টেন্ডুলকার। মা চাকরী করতেন ‘লাইফ ইনস্যুরেন্স কোর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া’তে। আজকের এই আমি হওয়ার জন্য এই দু’জন মানুষের কাছে ভীষণভাবে ঋণী আমি। আমার জন্য জীবনে অসংখ্যবার অনেক অনাকাক্সিক্ষত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছেন তারা। কিন্তু কোনবারই আমার উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যায়নি তাদের, বারবার সুযোগ করে দিয়েছেন আমাকে। সত্যি কথা বলতে, মাঝে মাঝে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে, আমার মত এতটা দুষ্টু ছেলের সাথে মা-বাবা পেড়ে উঠতেন কিভাবে। আমি জানি, অসংখ্যবার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছি আমি কিন্তু তারা আমার এসব দুষ্টুমী বা বেয়াদবীর সাথে ঠিকই মানিয়ে নিতেন। কিভাবে পারতেন জানি না, আমি তাদের জায়গায় থাকলে অবশ্যই পারতাম না। আমার বাবা কখনও রেগে কথা বলতেন না আমার সাথে। তিনি বোঝাতেন যে, কেন আমার ঐ কাজটা করা উচিত নয়। তার এই বোঝানোর ব্যাপারটা সবসময়ই অনেক বেশি কাজে লাগত। ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের সময় বাবাকে হারানো আমার জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনাগুলোর একটা। একজন মানুষ হিসেবে আজ আমি যেমন তার জন্য আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী বাবার কাছে।
আর আমার মা আমার হাসির জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। আমার কাছে আমার মা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাধুনী। মাছের তরকারী আমার মায়ের চেয়ে ভালো আর কেউ রাধতে পারবে না। তাছাড়া মাঝে মাঝেই মা বাড়িতে আমাদের জন্য বাইগান ভার্তা, বারান ভাত (মসূরের ডালের খিচুরী) রান্না করতেন। খাবারের প্রতি আমার যে ভালোবাসা এর পেছনের মানুষটা সম্ভবত আমার মা। আমার খুব মনে পড়ে, যখন ছোট ছিলাম তখন ভরপেট খেয়ে মায়ের কোলে শুয়ে থাকতাম। মা গান গেয়ে আমাকে ঘুম পাড়াতেন। দিনের শেষে মায়ের গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। এই ব্যাপারটা মনে হয় গানের প্রতি আমার নিগূঢ় টানের বীজ আমার মনের গভীরে রোপন করেছিল। গানের প্রতি এই প্রবল টান এখনও আমার আছে।
আমার দু’ভাইÑ নিতিন আর অজিত। অসংখ্যবার অসংখ্য অকাজ করে এসে এই দুই ভায়ের জন্য বেঁচে গেছি আমি। ক্রিকেটের ব্যাপারেও এই দু’জনের কাছে আমার অনেক ঋণী। অজিত ভাইয়া আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়। ক্লাব ক্রিকেটার হিসেবে ভালো নাম আছে। কিন্তু আমার জন্য ভাইয়া নিজের ক্রিকেট ক্যারিয়ারের বলি চড়িয়েছে। নিজে খেলা ছেড়ে আমাকে ভালো ক্রিকেটার বানানোর চেষ্টা করেছে। তার কাছে আমার ঋণ শেষ হবার নয়। শেষ টেস্ট ম্যাচের দিন বিদায় বক্তব্যে অজিত ভাইয়ার কথা বলেছিলাম আমি। একই স্বপ্নে বসবাস আমার আর অজিত ভাইয়ার। সারাটা জীবন নিজের একজন ভরসার সমালোচক হিসেবে পেয়েছি ওকে। এমনকি শেষ টেস্টে আউট হওয়ার পরেও আমরা বরাবরের মত আলোচনা করেছিলাম খেলার সময় কি কি ভুল ছিল, কোন ভুলের কারণে আউট হয়ে গেলাম। খেলায় ভালো করি আর খারাপ করি, সবসময়ই উৎসাহ জোগানোর জন্য অজিতকে পাশে পেয়েছি আমি। ও শুধু আমার ভাই নয়, আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। দরকারের সময় ওকে পাইনি এমন কখনও হয়নি আমার জীবনে। ওর কাছে আমার খেলাটা ওর নিজের যেকোন কাজের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সবসময়ই।
বড় ভাই নিতিন, পরিবারের সবচেয়ে সৃজনশীল, নিয়মনিষ্ঠ সদস্য। খুব ভালো স্কেচ করতে পারে। ইদানীং সাহিত্যিক হিসেবে নাম করেছে। চলচ্চিত্রের জন্য গানও লিখতে শুরু করেছে। প্রথমে রসায়নের শিক্ষক হিসেবে কাজ করলেও পরে এয়ার ইন্ডিয়ায় যোগ দেয় নিতিন। এয়ার ইন্ডিয়ার একটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। আমার বয়স যখন দশ তখন ভাইয়া এয়ার ইন্ডিয়ায় চাকরি করত। একবার ওর ফ্লাইট ডিলে হল। দেরী হওয়ার জন্য ওকে থাকতে দেয়া হল মুম্বাইয়ের দি সেনটর হোটেলে। দি সেনটর হোটেল এখন ‘সাহারা স্টার’ নামে সুপরিচিত। যাই হোক, ভাইয়া হোটেলে ছিল। তাই অজিত ভাইয়া আর আমি সন্ধ্যার দিকে গেলাম হোটেলে। সেখানে জীবনে প্রথমবারের মত তান্দুরী চিকেন খেয়েছিলাম। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তান্দুরী চিকেন আমার অন্যতম প্রিয় খাবার।
প্রথম ক্রিকেট ব্যাটটা পেয়েছিলাম আমার বোন সাবিতার কাছ থেকে। একবার কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে আমার জন্য ব্যাটটা নিয়ে এসেছিল আপু। তখন আমার বয়স পাঁচ। বেড়ে ওঠার সময় কোন ঝামেলায় পড়লে সাজেশনের জন্য যেতাম ওর কাছে। ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সত্যিই খুব মিস করতাম ওকে। ছোট বেলায় রীতিনীতি জিনিসটা খুব ভালো বুঝতাম না। তাই আপুর বিয়ের পর সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে, বিয়ের পর আপুর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার দরকার নেই, ওর স্বামীর উচিত আমাদের বাড়িতে চলে আসা। আসলে আমি চাইছিলাম না, আপু আমাদের ছেড়ে চলে যাক।
ছুটোছুটি
এককথায় বলতে হলে, অসাধারণ একটা শৈশব ছিল আমার। বিরক্তিকর সময় বলে কিছু ছিল না। প্রতিটা মূহুর্তই মজার।
আমার পরিবার সাহিত্যিক সাহাওয়াস কলোনীতে চলে আসে ১৯৭৩ সালে। ঐসময় ঐ এলাকায় প্রচুর কন্সট্রাকসন কাজ চলছিল। আমরা বন্ধুরা সবাই মিলে এই কন্সট্রাকসন সাইটগুলো থেকে বেশ কিছু মজার উৎস বের করে নিলাম। এইসব কথা মনে পড়লে এখন বেশ লজ্জাই লাগে।
এগুলোর মধ্যে একটা ছিল নির্মানাধীন বাড়িগুলোর আশে পাশে গর্ত খুড়ে তাতে লোকজনকে ফেলে দেয়া। ব্যাপারটা ছিল এরকম, প্রথমে মোটামুটি গভীর একটা গর্ত খোড়া হত। তারপর গর্তের মুখ খবরের কাগজ, গাছের পাতা ইত্যাদি আরো অনেককিছু দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হত যেন বোঝা না যায় যে ওখানে একটা গর্ত আছে। তারপর সবাই মিলে অপেক্ষা করতাম কখন একজন ঐ গর্তের ওপর দিয়ে যাবে আর ধপাস। ব্যাপারটা আমাদের জন্য অনেক মজার হলেও যে ব্যক্তি গর্তে পড়ত তার জন্য যে ব্যাপক বিরক্তিকর, ভয়ংকর, লজ্জার সেটা তো আর আলাদা করে বলতে হয় না। এখন ভাবলে খানিকটা অপরাধবোধ হয়। কিন্তু ঐ ছোটবেলায় ব্যাপারটা এতই উপভোগ্য ছিল যে, কখনও যদি অনেকক্ষণ বসে থাকার পরেও কেউ আমাদের ফাঁদে না পড়ত তাহলে আমরা লোকজনকে রীতিমত দাওয়াত দিয়ে এনে গর্তে ফেলতাম।
ঐ বয়সে আমাদের আরেকটা দুষ্টুমী ছিল, পাঁচ তলার উপর থেকে পথচারীদের ওপর পানি ঢেলে ভিজিয়ে দেয়া। আবার এলাকার যেসব গাছ থেকে ফল পাড়া নিষেধ ছিল সেসব গাছ থেকে ফল চুরি করে বেশি মজা পেতাম। আমরা, বিশেষ করে আমি। আবার মাঝে মাঝেই আমরা পাড়া-প্রতিবেশিদের অ্যাপার্টমেন্টের সদর দরজা বাইরে থেকে আটকে দিতাম। এর ফলে কারো জরুরী কাজে যেতে দেরী হলে আমাদের মজাই মজা।
আমার প্রথম স্কুল ছিল বান্দ্রাতেই। ইন্ডিয়ান এডুকেশন সোসাইটির নিউ ইংলিশ স্কুল। ছাত্র হিসেবে আমি কখনই প্রথম সারির ছিলাম না, আবার একেবারে শেষদিকের দলেও ছিলাম না। তবে স্কুল সব সময়ই মজার ছিল। স্কুলের খেলার নেশা এত বেশি ছিল যে, ছুটির দিনগুলোতে একেবারেই ভালো লাগত না। সকাল ন’টায় বাড়ি থেকে খেলতে বের হতাম, সারাদিন খেলতাম, সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফিরতাম। খাওয়া-দাওয়ার জন্যও ফিরতাম না সারাদিন। দেখা যেত বাড়ি থেকে কাজের লোকের মাধ্যমে খাবার পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি খেলায় মত্ত। তারপর পাশে বসে খেয়ে নিচ্ছি।
সন্ধ্যা পাড় হওয়ার পর আমার সঙ্গী সাথীরা সব ফিরে যেত তারপরও দেখা যেত আমি একা একাই খেলছি। সঙ্গী সাথী না পেলে মাঝে মাঝে একা একা খালি পায়ে পুরো কলোনী দৌড়ে বেড়াতাম।
এমন পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ সময়ই নিতিন ভাই আমাকে ডাকতে আসত। ডাকার জন্য নিতিন বাইকে পাঠানোর একটা কারণ ছিল, ওকে আমি বেশ ভয় পেতাম। এমনিতে ও কথাবার্তা বলত কম। কিন্তু ওর ওয়ার্নিং মানে ফাইনাল ওয়ার্নিং। তাই সঙ্গত কারণেই আমি ওকে সহজে ঘাটাতাম না। মাঝে মাঝে মা যখন আমার দুষ্টুমীগুলোতে বিরক্ত হয়ে যেতেন তখন নিতিন ভাইকে পাঠাতেন।
আমাদের বাড়িতে বেডরুম ছিল দু’টো। তাই আমরা চার ভাই বোন একঘরে ঘুমাতাম। ঘুমানোর সময় একেকদিন একেক দিকে মাথা দিতে ভালো লাগত আমার। ভালো লাগত মানে এটাও দুষ্টুমীর অন্তর্গত। আজ উত্তর মাথা দিলাম তো পরের দিন দক্ষিণে, আবার আরেকদিন মনে চাইলো তো পূর্বে বা পশ্চিমে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি যেদিকে মাথা দিয়ে ঘুমাবো অন্য ভাই বোনদেরও সেদিকে মাথা দিয়ে ঘুমাতে হবে। এই ব্যাপারটাই আমার কাছে মজার ছিল।
প্রথমবার চাইনিজ খাবার
আগেই বলেছি মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলো খুব ভালো রান্না করত মা। এই সুস্বাদু খাবার খেতে খেতেই খাবারের প্রতি ভালোবাসা জন্মে গিয়েছিল আমার। ভারতীয় খাবার বহুবার খেলেও, যখন প্রথমবারের মত চাইনিজ খাবার খেয়েছিলাম তখন আমার বয়স নয়। ১৯৮০’র দশকে মুম্বাইয়ে চাইনিজ খাবারের জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করে। হরহামেশাই লোকজনের মুখে চাইনিজ খাবারের গুণগাণ শোনা যেতে লাগলো। এইসব শুনে আমরা কলোনীর সব বন্ধুরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম চাইনিজ খেতে যাব।
যেই কথা সেই কাজ। চাঁদা তোলা হল। জনপ্রতি দশ রুপী। তখন আমার কাছে দশ রুপী মানে বিরাট ব্যাপার। এতগুলো টাকা দিতে বেশ কষ্ট হল কিন্তু নতুন কিছু করতে যাচ্ছি এজন্য বেশ এক্সাইটেড ছিলাম আমি। এখানে বলে রাখি, তখন আমি ছিলাম আমাদের গ্রæপের কনিষ্ঠতম সদস্য।
যাই হোক, বিরাট দল নিয়ে রেষ্টুরেন্টে গেলাম। লম্বা একটা টেবিলে বসতে দেয়া হল আমাদের। শুরুতেই “চিকেন এন্ড সুইটকর্ন স্যুপ’ অর্ডার দেয়া হল। হাতবদল হতে হতে স্যুপ শেষ পর্যন্ত যখন আমার কাছে আসল তখন গামলায় খুব সামান্যই স্যুপ অবশিষ্ট ছিল। তারপর ফ্রাইড রাইস আর চওমিনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। দু’তিন চামচ ভাগ্যে জুটল। বাহিনীর বড়রা বেশ ভালোভাবেই খেয়ে নিল আমাদের টাকায় আর আমরা পেটে ক্ষুধা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।
এই ছিল আমার প্রথম চাইনিজ খাবার অভিজ্ঞতা।

বাইসাইকেলের স্বপ্ন
বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, ছেলেবেলায় বেশ জেদী ছিলাম আমি। আমার বেশিরভাগ বন্ধুদেরই নিজেদের সাইকেল ছিল কিন্তু আমার ছিল না। তাই দেখানোর জন্য হলেও বাইসাইকেল একটা কিনতেই হবে। এদিকে আমরা কিছু চাইলে বাবা কখনই সরাসরি না করত না। বলত কয়েকদিন পর কিনে দেবে।
অন্যদিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মুম্বাই শহরে চার ছেলে-মেয়েকে লালন-পালন করা মা-বাবার পক্ষে মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু আমরা ভাই-বোনরা কখনই কোনরকম সমস্যা অনুভব করিনি। তবে বলাবাহুল্য মা-বাবা আমাদের চাহিদা পূরণ করতে সবসময়ই হিমশিম খেতেন। একবার বাইসাইকেলের ভুত মাথার উপর এতই বেশি সওয়ার হল যে, গোঁ ধরে বসলাম। বাড়ির সবাইকে বলে দিলাম যতদিন আমাকে বাইসাইকেল কিনে দেয়া হবে না, ততদিন ঘরের বাইরে যাব না। এখন মনে হলে নিজের কাছেই লজ্জা লাগে কিন্তু ঐসময় আমি সত্যি সত্যি টানা সাতদিন বাড়ির বাইরে বের হইনি।
এই সাত দিনের মধ্যে আরেক কাহিনী ঘটল। বাইরে না গিয়ে প্রতিদিন লম্বা একটা সময় আমি বারান্দায় গিয়ে বসে থাকতাম। বারান্দায় গ্রিল দেয়া ছিল। ছোট ছিলাম বলে গ্রিলের ওপর দিয়ে বাইরে দেখতে পারতাম না। কিন্তু বড়দের মত গ্রিলের উপর দিয়ে নিচের দিকে দেখার শখ আমার বহুদিনের। তো সেই শখ পূরণ করতে গিয়ে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে দিয়ে নিচের দিকে দেখতে লাগলাম। বেশ মজা লাগছিল। কারণ উপর থেকে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে লোকজনকে চলাফেরা করতে দেখা আমার জন্য পুরোপুরি নতুন অভিজ্ঞতা। এর আগে এই অভিজ্ঞতা নেয়া হয়নি কারণ এর আগে কখনও গ্রিলের ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে বাইরে দেখতে পারিনি আমি। কিন্তু সেদিন বহুদিনের অধ্যবসায়ের ফল পেলাম। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে বাইরে দেখতে পারলাম। কিন্তু বাইরের দৃশ্য দেখা শেষে মাথা যখন গ্রিলের ফাঁক থেকে বের করতে যাব তখন ঘটল বিপর্যয়। মাথা আর বের হচ্ছে না। কসরত করে ঢোকাতে পারলেও বের করার সময় আর কোন কসরতই কাজে লাগছিল না। প্রায় আধা ঘণ্টা নিজে নিজে মাথা বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। এসময় বাড়ির সবাই আমার মাথা আটকে যাওয়ার ব্যপারটা আবিষ্কার করল। সবাই মিলে অনেক চেষ্টা করে মাথায় তেল টেল লাগিয়ে গ্রিলের ফাঁক থেকে মাথা বের করে আনা গেল।
আমার এইসব কর্মকান্ড দেখে মা-বাবা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কয়েকদিনের মধ্যেই একেবারে ব্র্যান্ড নিউ একটা সাইকেল পেলাম আমি। নতুন সাইকেল দেখে একঘণ্টা গ্রিলের ফাঁকে আটকে থাকার কষ্ট উবে গেল। সাইকেল পাওয়ার সাথে সাথে চলে গেলাম বাইরে। নতুন সাইকেল বন্ধুদের দেখাতে হবে তো! সেই সাইকেল দেখাতে গিয়ে আরেক কাহিনী। প্রথম দিনই অ্যাক্সিডেন্ট। বাড়ির সামনে গলি দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছি। প্রথম তাই স্বাভাবিকভাবেই বেশ জোরে। একটা মোড়ের সামনে এসে এক সবজিওয়ালার ঠেলাগাড়ির সামনে মুখোমুখি সংঘর্ষ। সংঘর্ষের পর আমি যখন বাতাসে ভাসছি তখন আমার প্রথম অনুভূতিটা হল, “হায়! হায়! আমার নতুন সাইকেল!” একমূহুর্ত পর নিজেকে রাস্তার উপর আবিষ্কার করলাম। সাইকেলের দুটো স্পোক ডান চোখের একটু উপরে ঢুকে গেছে। রক্ত দিয়ে মাখামাখি কিন্তু এসব নিয়ে কোন দুঃখ নেই। দুঃখ হল, আমার ব্র্যান্ড নিউ সাইকেলটার সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।
আধা-ভাঙ্গা চেহারা আর পুরো ভাঙ্গা সাইকেল নিয়ে গেলাম বাসায়। আমাকে দেখেই সবাই হায় হায় করে উঠল। আমি একটু সাহস দেখিয়ে বললাম, “আরে সামান্য চোট। এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে।” কিন্তু চোট সামান্য ছিল না। বাবা আমাকে এক প্লাস্টিক সার্জনের কাছে নিয়ে গেলেন। সেই সার্জন আবার ছিল বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ডাক্তার চাচা ডান চোখের উপরে খুব যতœ করে আটটা সেলাই আর গোটা কয়েক ইনজেকশন দিয়ে দিলেন। এসব নিয়ে বাবা আমাকে কিছুই বললেন না। শুধু বললেন, সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাকে যেন সাইকেলের আশেপাশেও না দেখা যায়। এরমধ্যে আমার সাইকেলও সারিয়ে দেবেন বলে জানালেন।
সুস্থ হতে খুব বেশিদিন লাগলো না। আমার সাথে সাথে আমার সাইকেলও সুস্থ হয়ে উঠলো। তো আবার শুরু হল সাইক্লিং। কিছুদিনের মধ্যেই আমি বেশ দক্ষ সাইক্লিস্ট হয়ে উঠলাম। আমার কলোনীতে আমার চেয়ে ধীরে কেউ সাইকেল চালাতে পারতো না। স্থানীয়ভাবে আয়োজিত যে কোন রেসেও আমার সাথে পেড়ে উঠতো না কেউ। কয়েকমাসের চেষ্টায় এক চাকার ওপর ভর করে সাইকেল চালানোর কায়দাটা রপ্ত করে ফেললাম। আবার রাস্তার ওপর দশ-পনের ফুট ¯øাইড করতেও শিখে গেলাম। এইসব ¯øাইড করতে গিয়ে টায়ারের কি অবস্থা হত এসব নিয়ে কোন মাথাব্যথাই হত না। ¯øাইড করে যত বেশি দূরত্ব কভার করতে পারতাম তত খুশি লাগত। আমার বন্ধুরাও আমার এসব কারসাজি দেখে অবাক বনে যেত। তারা যত অবাক হত আমার আত্মতৃপ্তি তত বাড়ত।
মাঝে মাঝেই এসব করতে গিয়ে ব্যথা পেতাম। কিন্তু প্রেসটিজের ব্যাপার। ব্যথা সহ্য করে আবার করে দেখাতাম। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটত। তাই সবসময়ই তো বাসায় গিয়ে বলা সম্ভব না যে, ‘ব্যথা পেয়েছি’। তো আমি গোপন করে যেতে লাগলাম। কিছু দিনের মধ্যেই বাবা ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লে মাঝে মাঝে বাবা আমার সারা শরীর পরীক্ষা করে দেখতেন। কোথাও যদি বড় কোন আঘাতের লক্ষণ দেখতেন পরদিন নিয়ে যেতেন ডাক্তারের কাছে। ব্যথা আমলে না নিয়ে কাজ করে যাওয়ার যোগ্যতাটা ক্রিকেট ক্যারিয়ারে অনেক সাহায্য করেছে আমাকে। এই যোগ্যতাটা বোধহয় আমি এভাবেই পেয়েছি।
আমি যা কিছুই করি না কেন বাবা কখনই কোনরকম রাগারাগি করতেন না। সুন্দর করে বোঝাতেন যে, কেন আমার ঐকাজটা করা উচিত নয়। আর কেন উচিত নয় এর এত কারণ সামনে তুলে ধরতেন যে পরবর্তীতে সেই কাজটা আর করতে ইচ্ছে করত না। আমার কাছে বাবার এই যোগ্যতাটা অসাধারণ লাগত। আমার সন্তানদের ক্ষেত্রেও আমি একই কাজ করার চেষ্টা করি সবসময়।
ঝামেলার পর ঝামেলা
শিবাজী পার্ককে মুম্বাই ক্রিকেটের আতুড়ঘর বললেও ভুল হয় না। আমার বয়স তখন বারো। শিবাজী পার্কে ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল। আমার দলের ক্যাপ্টেনের দায়িত্বে ছিলাম আমি। খেলার এক পর্যায়ে আমাদের উইকেট-কীপার ব্যথা পেল। উইকেট কীপিং করার মত কাউকে পাওয়া গেল না। নিজেই গেলাম কীপিং করতে। এর আগে কোনদিন এই কাজ করিনি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বল এসে লাগলো চোখের নিচে। রক্ত বের হতে শুরু করল।
আহত হয়ে বিদায় নিলাম। টেক্সি নিয়ে বাসায় ফেরার মত টাকা ছিল না কাছে। দু’য়েকজন বন্ধুকে বললাম সাইকেলে করে বাসায় পেঁছে দিতে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কেউ রাজি হল না। যারা মুম্বাইয়ের রাস্তায় চলাফেরা করেছেন তারা জানেন মুম্বাইয়ের ব্যস্ত রাস্তায় সাইকেল নিয়ে একা চলাই কষ্ট সেখানে ক্রিকেটের সরঞ্জামসহ আরেকজনকে নিয়ে যাওয়া অনেক বেশি কঠিন কাজ। তাই সাইকেলে পৌঁছে দিতে রাজি না হওয়াটাই সঙ্গত। আবার রক্তমাখামাখি অবস্থায় বাসে ওঠাও সমস্যা। তাই হেটেই রওনা হলাম। রাস্তার লোকজন সব ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখছিল। ঐসময় মুম্বাইয়ের রাস্তায় ক্রিকেটের পোশাক গায়ে রক্ত-মাখা চেহারার কিশোরের হেটে যাওয়ার দৃশ্য মোটেই প্রতিদিনকার ছিল না। তাই লোকজন আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক ছিল, যদিও আমার যারপরনাই বিরক্ত লাগছিল।
খেলতে গিয়ে এরকম আহত বহুবার হয়েছি আমি তার সবগুলোর বিবরণ দিয়ে পাঠককে বিরক্ত করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

গান : আমার দ্বিতীয় ভালোবাসা
টেন্ডুলকার পরিবারের সবাই কমবেশি গান পছন্দ করত। বড়রা নিয়মিত বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠান শুনত। তো স্বাভাবিক ভাবেই ছোটবেলায় খুব বেশি বোঝার বয়স হওয়ার আগেই গানের প্রতি ভালোলাগার জন্ম হয় আমার মধ্যে।
বাড়ির সবার গানের প্রতি ভালোবাসা আরেক ধাপ বেড়ে গেল যখন বাবা একটা ক্যাসেট-প্লেয়ার কিনে আনলেন এবং সবাইকে যার যার পছন্দমত গান শোনার অনুমতি দিলেন। আমার দুই ভাই পঙ্কজ উদাসের গজলের খুব বড় ফ্যান। তাই নিয়মিত পঙ্কজ উদাসের গজল শোনা হত আমাদের বাড়িতে। গান নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা চলত বড়দের মাঝে, আর হা করে তাদের কথা শুনতাম আমি।
আমার খুব ভালো মনে আছে, নিতিন ভাইয়া একবার দুবাই গেল। আসার সময় পঙ্কজ উদাসের নতুন একটা অ্যালবাম নিয়ে ফেরার কথা ছিল ওর। ভাইয়া ফিরতে ফিরতে মধ্যরাত হয়ে গিয়েছিল, আমরা সবাই মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম নতুন অ্যালবাম শোনার জন্য। ফেরার পর নতুন অ্যালবাম বাজিয়ে শুনতে শুরু করলাম সবাই। শুনতে শুনতে একসময় দেখি দাদী মা সকালের চা নিয়ে এসেছে সবার জন্য। মানে গান শোনার জন্য একটা নির্ঘুম রাত পাড় হল আমাদের।
এই পরিবেশে থাকলে, গানের প্রতি ভালোবাসা জন্মানোই স্বাভাবিক। তো স্বাভাবিকভাবেই গান আমার দ্বিতীয় ভালোবাসায় পরিণত হল। সবধরনের গানই শুনতে ভালো লাগে। মোটামুটি সবধরনের হিন্দি গান, সিনেমার গান, ইংরেজি গান শোনা হয়। কানে হেডফোন দিলে সবসময় রিল্যাক্সড ফিল করি। কৈশরের পর থেকে ওয়েস্টার্ন গানের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। পিংক ফ্লয়েড, ইউটু, ডায়ার স্ট্রেইট ইত্যাদি অনেক ব্যান্ডের গান ভালো লাগে। আমার এই ওয়েস্টার্ন মিউজিক প্রীতি ধীরে ধীরে অজিতের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এখন বাড়ির কমবেশি সবার মধ্যে ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।ৎ

ক্রিকেটের দিকে
ক্রিকেট আর গানের পাশাপাশি ছোটবেলায় টেনিসও খুব পছন্দ করতাম। কিংবদন্তী আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড় জন ম্যাকেনরো’র খুব বড় ফ্যান ছিলাম। এত বড় ভক্ত ছিলাম যে, মাত্র দশ বছর বয়সে ম্যাকেনরোর মত বড় বড় ঝাঁকড়া চুল রেখেছিলাম, হাতে সবসময় তার মত একটা হ্যান্ডব্যান্ড লাগিয়ে ঘুরতাম। কোন কোন ক্ষেত্রে পছন্দের বেলায় ক্রিকেটের চেয়ে টেনিস অনেক বেশি এগিয়ে থাকত আমার কাছে।
অজিত ভাইয়া না থাকলে হয়তো ক্রিকেটার না হয়ে টেনিস খেলোয়াড় হয়ে যেতাম। ওর ধারণা ছিল ঠিকমত ট্রেনিং দেয়া হলে অনেক ভালো ব্যাটসম্যান হওয়ার যোগ্যতা আছে আমার মধ্যে। অজিত ভাইার কারণেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, টেনিসের চেয়ে ক্রিকেটটা অনেক বেশি উপভোগ করি আমি। এই অজিত ভাইয়াই আমাকে প্রথম রামাকান্ত আক্রেকার স্যারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। রামাকান্ত স্যারের কাছে ট্রেনিং শুরু করার সময় আমার বয়স ছিল মাত্র এগারো। অজিত ভাইয়া না থাকলে হয়তো আমার রামাকান্ত স্যারের কাছে যাওয়াই হত না, ক্রিকেটার হওয়াও হত না। এখানে একটা কথা না বললেই নয়, রামাকান্ত স্যারের ক্রিকেট ক্যাম্প থেকে মুম্বাইয়ের অনেক নামী-দামী ক্রিকেটার উঠে এসেছে।












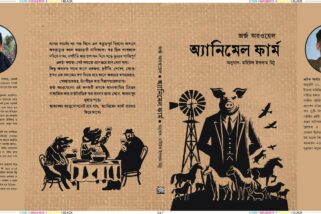











 লেখার চেষ্টা করছি।
লেখার চেষ্টা করছি।